রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য ভাবনা - সাহিত্য ও সাহিত্য সৃষ্টি প্রবন্ধ এর আলোকে
মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, 01789-699509
তথ্য বিনির্ভর, যুক্তিরিক্ত, ব্যক্তিরস ও ব্যক্তি স্বগত গুঞ্জরনমুখ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের(১৮৬১-১৯৪১) প্রবন্ধগুলোতে পাওয়া যায় কবির সৃজনশীলতা, কল্পনারস, ব্যক্তিক আবেগ ও একই সাথে প্রাবন্ধিকের চিন্তার গভীরতা ও সৃজনশীলতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য ভাবনা কয়েকটি নয় অসংখ্য প্রবন্ধে লুক্কায়িত। তার সাহিত্য, সাহিত্য সৃষ্টি, সাহিত্যের পথে, সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্যতত্ত্ব প্রমুখ প্রবন্ধে তার সাহিত্যচেতনার নানা দিক প্রকাশিত হয়েছে। তিনি সাহিত্যকে দেখেছেন এক শিল্পিত এক প্রকাশ হিসাবে।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য ভাবনা - সাহিত্য ও সাহিত্য সৃষ্টি প্রবন্ধ এর আলোকে - part 1
সাহিত্যের মাঝে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন চিরকালীনতা, বহুর সাথে ঐক্যকে, মানবহৃদয় বা পাঠক হৃদয়কে। মানবমনের বিক্ষিপ্ততাকে সাহিত্য একতা দিতে পারে। এ প্রসঙ্গে বেগম আকতার কামাল বলেন-
“... সাহিত্যে রূপের মধ্যে বিশৃঙ্খল বহুধাবিভক্ত অবিন্যাসকে ধরা যায়, তাৎপর্যের ঐক্যে বিন্যাস করা যায়।”
(বেগম আকতার কামাল, যেথায় যত আলো, ১ম প্রকাশ ২০১৪, পৃ.২৯)
সাহিত্য সৃষ্টি ও মানুষের মাঝের যোগবন্ধন, আনন্দের প্রকাশ। এটি আনন্দের প্রকাশ বলেই তা চিরকালীন ও সার্বজনীন। যুগের সাথে সাথে লেখক ও পাঠকের চাহিদায় তা পরিবর্তিত হয়, পরিমার্জিত হয় ও সংযোজিত হয়।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য ভাবনা - সাহিত্য ও সাহিত্য সৃষ্টি প্রবন্ধ এর আলোকে - part - 2
১৩৩০ ও ১৩১৪ সালে প্রকাশিত তাঁর ‘সাহিত্য’ ও ‘সাহিত্য সৃষ্টি’ প্রবন্ধে তিনি নানা সাহিত্যিক কর্মের উদাহরণ দ্বারা সাহিত্যের তাৎপর্য, তার প্রকাশতত্ব এর সৃষ্টির পেছনের নানা স্তর এবং সৃষ্টি হবার পর তাঁর নানা বাঁক-বদল নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর এই দুটি প্রবন্ধে সাহিত্য সংক্রান্ত যে ধারণা পাওয়া যায় তাতে স্পষ্ট হয় তিনি সাহিত্যভাবনাতে উপনিষদীয় বাণী দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ব্রহ্মের নানা স্বরূপ কিংবা বৈষ্ণবীয় উদাহরণকে তিনি বাদ দিতে পারেননি। তাঁর কাছে শিল্প-সাহিত্যে মানব হৃদয়ের অসীমতা সীমার মাঝে ধরা দেয়।
১৩১৪ সালে রচিত ‘সাহিত্যসৃষ্টি’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে সাহিত্য সৃষ্টির নানা স্তরকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি প্রথমেই গুরুত্ব দিয়েছেন মানবমনে আসা নানা ভাবনার একটি নির্দিষ্টতাকে। মনের মাঝে ভাবনা অনেক হলেও সমজাতীয় ভাবনা কোনো একটি উদ্দীপনাকে কেন্দ্র করে তাহার চারিদিকে দানা বাঁধিয়া ওঠে। এই সকল দানা বাঁধা ভাবনার সকলই টিকে থাকে না। কেবলই জোরাল ভাবনাগুলো পরিপক্ক কাঁঠালের মতন পাকা কাঁঠাল হয়ে ওঠে। শুধু ভাবনা পরিপক্ক হলেই তার শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এই ভাবনাকে সাহিত্যরূপে পাঠকের মনে বোপিত হয়ে তাদের মনক্ষেত্রে নতুন ভাবনার উদয় ঘটানোই এর সার্থকতা। তাই ভাবনা বলে-
“এবার বিশ্বমানবের মনের ভূমিতে নবজন্মের এবং চিরজীবনের লীলা করিতে বাহির হইব।”
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য ভাবনা - সাহিত্য ও সাহিত্য সৃষ্টি প্রবন্ধ এর আলোকে - part - 3
ভাবনা সাহিত্যকে প্রথম আকার দিলেও তাকে হতে হয় পাঠক এর কাছে গ্রহণযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন বন্ধুভেদে যেমন আমাদের আলোচনার বিষয় পরিবর্তিত হয় তেমনি সাহিত্য সৃষ্টি হয় পাঠকদের গ্রহণ করবার ধারণ করবার ও বোধগম্যতার উপর। পাঠকের মনের প্রকৃতির সাথে মিলিয়ে লেখক তার সৃজনকে রূপ দেবেন। সাহিত্য শুধু লেখকের গুণে নয় যাদের জন্য লেখা তাদের গুণেও টিকে থাকে। যতদিন তা ভাবনা ছিল ততদিন তা নিজেস্ব ছিল। যখনই তা প্রকাশিত হল তখন তা একার সম্পত্তি নয় সবার সম্পদ হল-
“এমনি করিয়া সাহিত্য কেবল লেখকের নহে যাহাদের জন্য লিখিত তাহাদেরও পরিচয় বহন করে।”
সাহিত্য ভাবনাকে গ্রাস করে। শুধু নিজের নয় যুগের পর যুগ ধরে টুকরো টুকরো মানুষের যে ভাবনা ছিল তা কোনো একটি সাহিত্য ধারণ করে। সাহিত্যের এই ভাবনার সার্বজনীনতা অনেক সময় তৈরি করে মহাকাব্য। এ মহাকাব্য শুধু লেখকের একার নয় পুরো জাতির। রাম সম্পর্কিত টুকরো টুকরো গাঁথা, গল্পকে রামায়ণ ধারণ করেছে। মহাভারত, ইলিয়ড অডিসিও একইভাবে জাতির চেতনাকে ধারণ করেই সৃষ্টি। সাহিত্য তাই সকল মানুষের অবদান বলে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য ভাবনা - সাহিত্য ও সাহিত্য সৃষ্টি প্রবন্ধ এর আলোকে - part - 4
সাহিত্যকে তিনি তখনি খাঁটি বলেন যখন তা অন্য সাহিত্য হতে নানা ভাব গ্রহণ করে এবং তা পরিবর্তিত হয়। যে সাহিত্য গ্রহণ ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায় না তাকে সজীব বলার পক্ষপাতী নন প্রাবন্ধিক।
“... যাহার আর কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা নাই, তাহাকেই যদি খাঁটি জিনিস বলা হয়, তবে সজীব প্রকৃতির মধ্যে সে জিনিসটি কোথাও নাই।”
তিনি রামায়ণ হতে উদাহরণ দিয়ে বলেছেন রামায়ণের আদিকবি বাল্মিকীর হাতে যেমন ধর্মীয় আদর্শে রচিত কৃর্ত্তিবাসের কাছে তা মানবীয়। অন্যদিকে মাইকেল মধুসূদন তাকে সমকালীন উপনিবেশিকতার দৃষ্টিতে দেখেছেন একদম নতুন আঙ্গিকে। রামচন্দ্র যেমন অনার্যদের বশ করে, তাদের সাথে যুদ্ধ না করে মিলন ঘটিয়েছেন তেমনি সাহিত্যেও সকল দ্বন্দ্ব ভুলে মিলনকে স্বাগত জানাতে চান তিনি।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য ভাবনা - সাহিত্য ও সাহিত্য সৃষ্টি প্রবন্ধ এর আলোকে - part - 5
সাহিত্য রচনার ধারা সমকালীন প্রভাব মুক্ত নয়। রামায়ণ রচনায় সীতার জন্ম কোনো উদ্দেশ্যবিহীন ঘটনা নয়। কৃষি সমাজের বিস্তারের প্রতিনিধি ছিল লাঙ্গলের ফলা হতে জন্ম নেওয়া সীতা, শ্রীচৈতন্য দেবের বৈষ্ণব প্রেমলীলার বাংলা সাহিত্যের একটি ধারাই তৈরি হয় জীবনী সাহিত্য নামে রচিত হয় নানা বৈষ্ণবীয় ধারার কবিতা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-
“বর্ষা ঋতুর মতো মানুষের সমাজে এমন এক-একটা সময় আসে যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুররূপে বিচরণ করিতে থাকে।”
এই কালের হাওয়ার প্রভাবেই চৈতন্য পরবর্তী সাহিত্যে প্রেমরস থাকে। মাইকেল ভিন্ন আঙ্গিকে রামায়ণকে উপস্থাপনা করেন।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য ভাবনা - সাহিত্য ও সাহিত্য সৃষ্টি প্রবন্ধ এর আলোকে - part - 6
সাহিত্য সৃষ্টিতে কবি বারবার বিকাশের আগে প্রকাশকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর কাছে ভাবনার প্রকাশ না হলে তা সাহিত্য নয়। আসলে সাহিত্য যদি বাক্সবন্দি বা মনবন্দি হয় তবে তা কখনোই শিল্প হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রবন্ধেও তাঁর প্রকাশতত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন।
‘সাহিত্য’’(১৩৩০) প্রবন্ধে তিনি সাহিত্যের প্রকাশতত্ত্বকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। সাথে সাহায্য নিয়েছেন উপনিষদীয় বাণীর। তাঁর কাছে সাহিত্যের ঠানগুলো ব্রহ্মের তিন সত্তার সাথে সম্পর্কিত। উপনিষদে যেমন ব্রহ্মার স্বরূপের তিন ভাগ ১. সতম - আমি আছি, ২. জ্ঞানময় - আমি জানি ও ৩. অনন্তম - আমি প্রকাশ করি। নিজ অস্তিত্বের জানান দেয় ‘আছি’ সত্তা। সেই অস্তিত্বকে বজায় রাখতে আমরা ‘জানি’ সত্তাকে ব্যবহার করি। সে জানা স্থুল জানা। কীভাবে বংশবৃদ্ধি করতে হয় বা কীভাবে বেঁচে থাকার রসদ পেতে হয় এই সকল ‘'জানি’ সত্তার কাব্য। কিন্তু যখন তা কেউ অন্যের অস্তিত্বের মাঝে নিজের অস্তিত্বকে জানান দিতে পারে তখন মানুষে মানুষে যে বিচ্ছিনতা বোধ ছিল তা ঐক্যে রূপান্তরিত হয়। এটি কবির কাছে ‘'আত্মার ঐশ্বর্য’।
মিলনের প্রেরণার এই আনন্দ নানাভাবে প্রকাশিত হয়। তার সেই প্রকাশই সাহিত্য। প্রকাশটি শুধু মানুষের হয় পশুর প্রকাশ ক্ষমতা নেই বলেই মানুষ পশু হতে শ্রেষ্ঠ। মানুষের কাছে শুধু প্রাণধারনাই সব নয়। যখন মানবহৃদয় প্রকৃতির বিচিত্র লীলা হতে কিছু সংগ্রহ করে তা নিজের প্রয়োজন মিটিয়েও দান করতে পারে সেটিই হয় তার আত্মার ঐশ্বর্য বা প্রকাশ। ব্রহ্ম নিজেও চান প্রকাশিত হতে। প্রকাশেই তার আনন্দ। প্রকাশিত হতে চান বলেই তিনি এক হতে বহু হয়েছেন। তেমনি মানুষও তার সকল দীনতা পূরণ করে বাস্তব ঐশ্বর্যকে সাহিত্যের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে।
“যাকে নিজেই সম্পূর্ণ শোষণ করে নিয়ে নিঃশেষ না করিতে পারি, তাই দিয়েই তো প্রকাশ।”
প্রকাশ করা এই রূপটিই শিল্প যার মাঝে থাকে সাহিত্য।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য ভাবনা - সাহিত্য ও সাহিত্য সৃষ্টি প্রবন্ধ এর আলোকে - part - 7
প্রকাশই একমাত্র মাধ্যম যার মাঝে মানুষ টিকে থাকতে পারে। সাজাহান তার সিংহাসনে শক্তিমত্তা দেখিয়েছে ঠিকই কিন্তু তা তাঁর ‘'আছি’ সত্তার রূপ বলে ইতিহাস তাকে মানবহৃদয় পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। কিন্তু মমতাজের প্রতি তাঁর ভালোবাসা যখন তার হৃদয় তার ধারণ করতে পারেনি তখন তিনি তাঁর প্রকাশ করেছেন তাজমহলে। এই প্রকাশই তাকে ও তাঁর ভালোবাসাকে করেছে অমর। সাহিত্যেও পরিপূর্ণতার উপলব্ধি তাই-
“সর্বজনের ও নিত্যকালের হাতে তাকে সমর্পণ করা ছাড়া আর গতি নেই।”
তার জন্যই কালিদাসের যক্ষের বিরহ আজ বৈজয়নীর একার হয়ে থাকেনি। মেঘদূত বিক্রমাদিত্যের কড়া পাহাড়াকে অতিক্রম করতে পেরেছে কেবল তার প্রকাশ শক্তির গুণে। মানবহৃদয় ব্যাকুল থাকে ব্যক্ত হবার জন্য। ‘'সাহিত্যতত্ত্ব’ প্রবন্ধে কবি বলেন-
“শাস্ত্রে আছে, এক বললেন বহু হব। নানার মধ্যে এক আপন ঐক্য উপলব্ধি করতে চাইলেন”
প্রকাশ তার কাছে অমৃত। এই অমৃত দুই অর্থেই যেমন মৃত্যুহীন অর্থে তেমনি পরম রস বা আনন্দ অর্থেও। প্রকাশ তখনই হয় যখন মানবহৃদয় তার সৃজনের আনন্দকে আর ধারণ করে রাখতে পারে না। এই আনন্দের প্রকাশই সাহিত্য। এই আনন্দময়ী সাহিত্যই তখন হবে মৃত্যুজয়ী বা অমৃত-
“... রূপদক্ষ হয়-রূপ রচনা করেন, সেটি যদি আনন্দের প্রকাশ হয় তবে সে মৃত্যুজয়ী।”
এর জন্য কোনো শিল্পিত মাধ্যমের শ্রবণ, দর্শন বা অনুভব এর যে অনুভূতি তা সাথে সাথেই শেষ হয় না। এর ভেতরকার তত্ত্ব আমাদের ভাবায়। প্রয়োজনকে ছাপিয়ে তা অমর হয়। প্রক্ষের সম্মিদানন্দ রূপের মতনই সত্য বা চিত্তের চেয়ে প্রকাশের আনন্দটিই সর্বশেষ কথা। প্রকাশের এই আনন্দকে উপকার বা সুবিধার মাপকাঠিতে স্থাপন করা যায় না।
চিরকালই মানুষের মাঝে নিজের ভাব, আবেগ ও অনুভূতিকে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার তাগিদ ছিল। সেই তাগিদেই মানুষ ভেবেছে তার ভাবনাকে আকার দিয়ে তা পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। সেই পৌঁছানো যেমন তেমন নয় তা পাঠক হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক ঘটায়। সাহিত্যও মানুষের ভাবনার ফসল, প্রকাশের সাথে সাথে পাঠক হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভের বস্তু। সাহিত্য কোনো জৈবিক প্রয়োজনের বস্তু নয় তা বিশুদ্ধ আনন্দ। সকল বিচ্ছিন্ন্তার অন্তরতম ঐক্য।


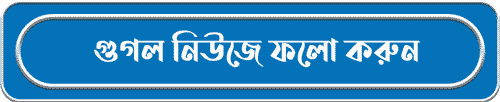
The DU Speech-এর নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন, প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়
comment url